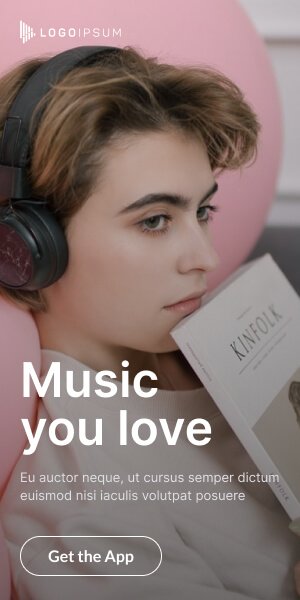ভারতের ২০২১ সালের নারী লাঞ্ছনার ভিডিওকে বাংলাদেশের বলে ছড়ানোর গুজব ভাঙল বাংলাফ্যাক্ট
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)–এর ফ্যাক্ট-চেক ইউনিট ‘বাংলাফ্যাক্ট’ জানিয়েছে, ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি নারী নির্যাতনের ভিডিও বাংলাদেশের নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের। ভিডিওটি ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটির একটি ক্লাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার সহযোগীদের হাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার। চলতি সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওটি শেয়ার করে দাবি করা হচ্ছিল, এটি নাকি ‘অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার’ সময়ে বাংলাদেশের ঘটনা—যা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার গুজব উসকে দেয়। reverse image search ও ভারতীয় মিডিয়া দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-সহ একাধিক সূত্র মিলিয়ে বাংলাফ্যাক্ট বিভ্রান্তিকর প্রচার চিহ্নিত করেছে। ২০২১ সালে ওই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছিল। বাংলাফ্যাক্ট বলছে, যেকোনো শেয়ার করার আগে ব্যবহারকারীদের উৎস যাচাই করা জরুরি।
প্রেক্ষাপট
গত কয়েক দিনে ফেসবুক, এক্স ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ঘুরছিল, যেখানে দেখা যায় এক নারীকে লোকজন ঘিরে মারধর করছে। ক্যাপশন ছিল, ‘ইউনূস সরকারের সময়ে নারীর ওপর নির্যাতনের ঘটনা, প্রমাণ লুকাতে চেষ্টা চলছে’। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আলোচনায় ‘অন্তর্বর্তী সরকার’ ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ইউনূসকে ঘিরে নানা গুজব ছড়াচ্ছে; সেই স্রোতেই ভিডিওটি ব্যবহার করা হয় বলে অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।
বিশ্লেষণ
বাংলাফ্যাক্ট ভিডিওর কয়েকটি কী-ফ্রেম আলাদা করে গুগলের reverse image search চালায়। মিল পাওয়া যায় দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে ৯ জুলাই ২০২৪-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের ছবির সঙ্গে। প্রতিবেদনে লেখা, ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহ তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘটে। তৎক্ষণাৎ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করেছিল এবং ভুক্তভোগী নারীকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের কোনো আইনি নথি, গণমাধ্যম রিপোর্ট বা পুলিশ রেকর্ডে এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ নেই। ফলে ভিডিওটি বাংলাদেশের বলে দাবি করা ‘মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’—বলছে বাংলাফ্যাক্ট।
প্রতিক্রিয়া
বাংলাফ্যাক্টের প্রধান গবেষক শাহীন মাহমুদ বলেন, ‘বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সামাজিক উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎস না দেখে শেয়ার করা বিপদজনক।’ ডিজিটাল নিরাপত্তা অধিদফতর জানিয়েছে, তারা বিষয়টি নজরে রেখেছে এবং প্রয়োজনীয় হলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ড. ইউনূসের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘গুজব দিয়ে ব্যক্তিগত ইমেজ নষ্ট করার প্রবণতা নিন্দনীয়।’
বৃহত্তর চিত্র
বাংলাদেশে নির্বাচন সামনে রেখে সামাজিক মাধ্যমে ভুল তথ্যের প্রবাহ বেড়েছে। সাইবার সিকিউরিটি সেলের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন মাসে নির্বাচনী প্রসঙ্গ ঘিরে ১২০টির বেশি ভুয়া ছবি ও ভিডিও শনাক্ত হয়েছে, যার ৪০ শতাংশই বিদেশি ঘটনার চিত্র। গবেষকেরা বলছেন, ভাষা ও ভৌগোলিকসীমা কাছাকাছি হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক ভিডিও বাংলাদেশে সহজেই খাপ খেয়ে যায়। সীমান্ত জেলায় একই টেলিভিশন চ্যানেল দেখা যায়, ফলে বিভ্রান্তি আরও বাড়ে।
পরবর্তী পদক্ষেপ
বাংলাফ্যাক্ট বলছে, সন্দেহজনক ভিডিও পেলেই তারা ‘মাল্টি-সোর্স’ যাচাই চালাবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফল প্রকাশ করবে। সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ‘গুজব শনাক্ত চেকলিস্ট’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে, যেখানে পাঁচটি সহজ ধাপ—উৎস, তারিখ, লোকেশন, মিডিয়া রিপোর্ট এবং স্বাধীন আরেকটি সূত্র—খতিয়ে দেখতে পরামর্শ দেওয়া হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোকে বিভ্রান্তিকর পোস্ট দ্রুত চিহ্নিত করতে স্থানীয় ফ্যাক্ট-চেকারদের সঙ্গে সমন্বয়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।